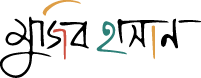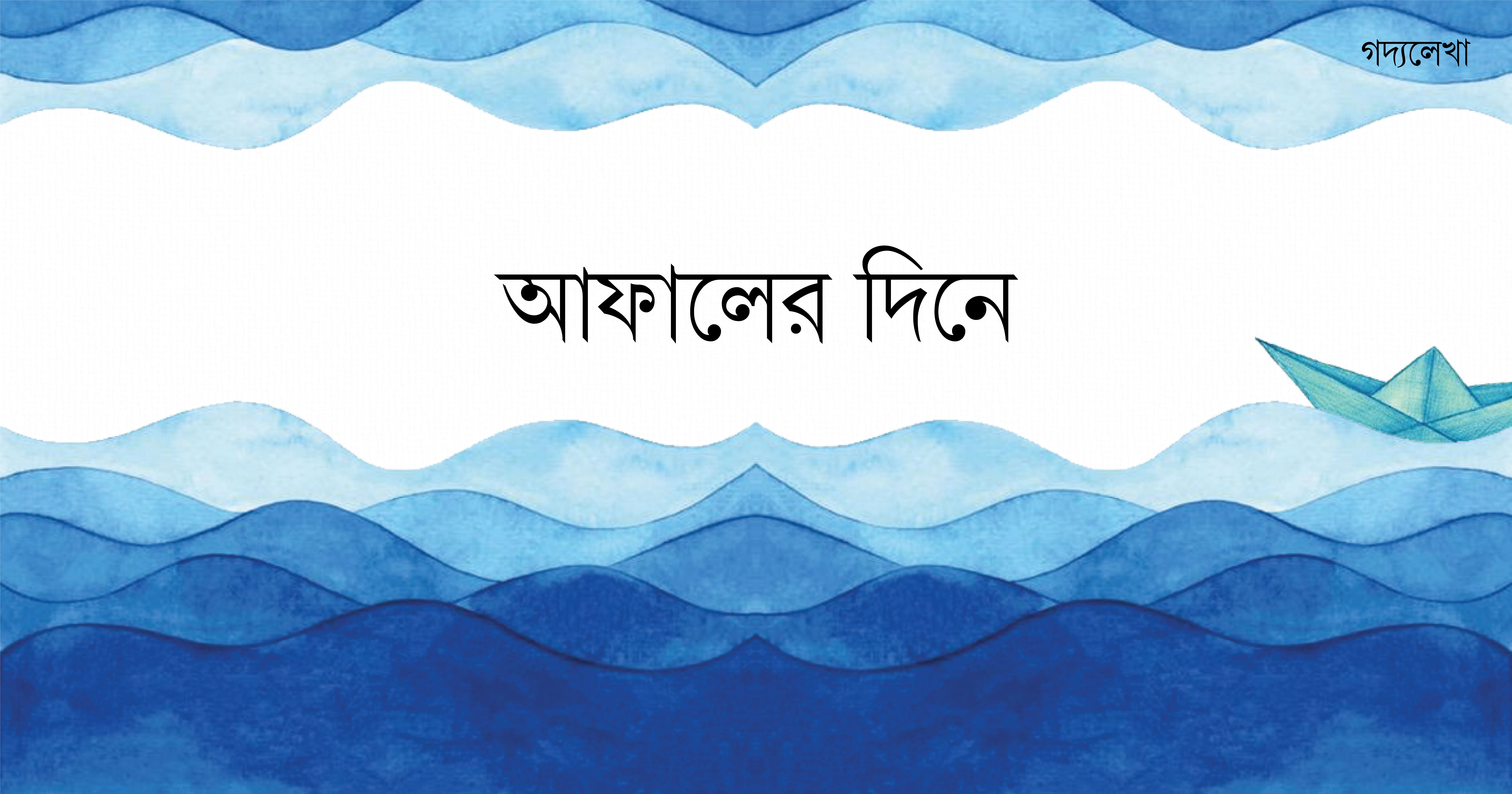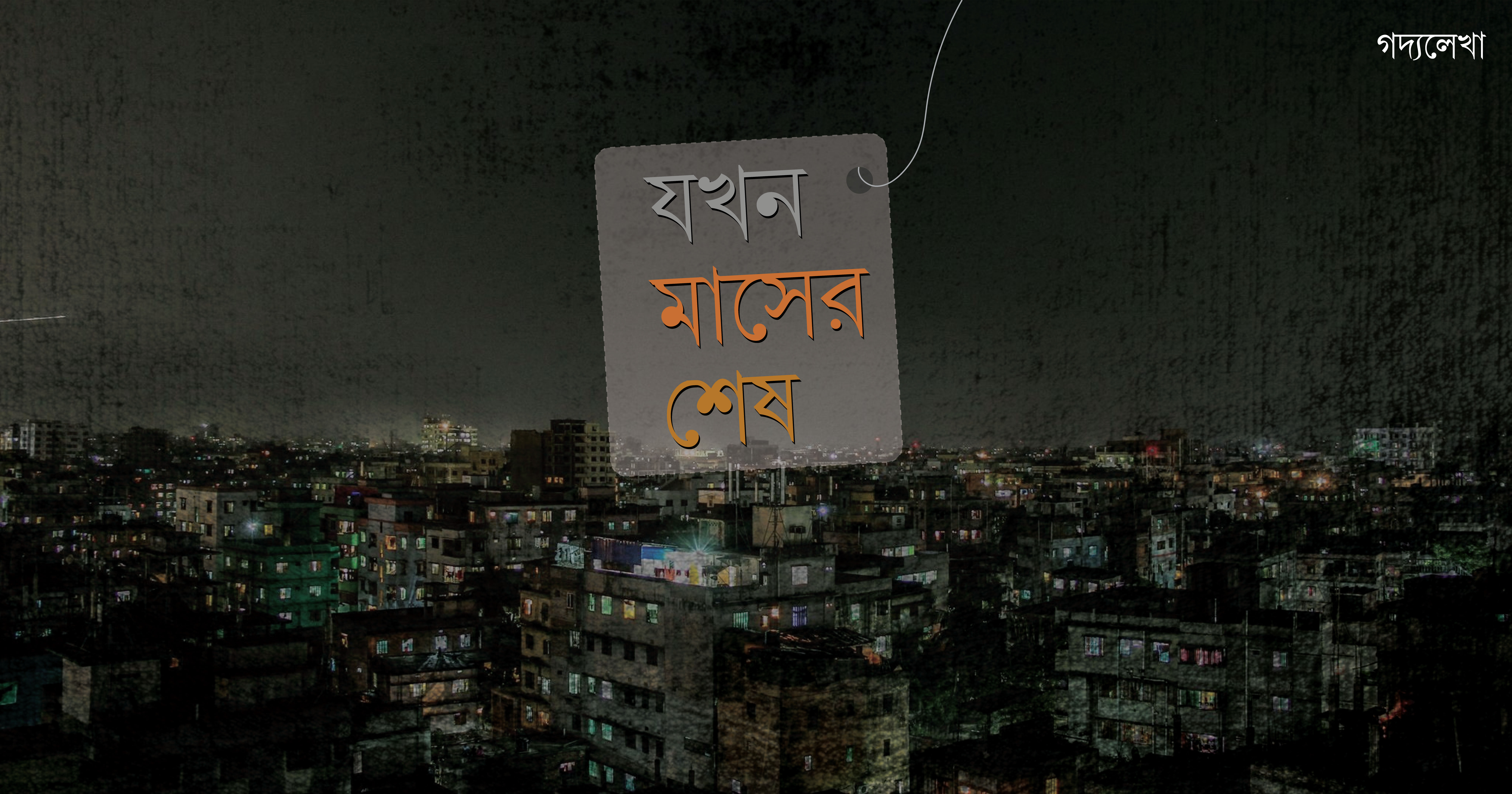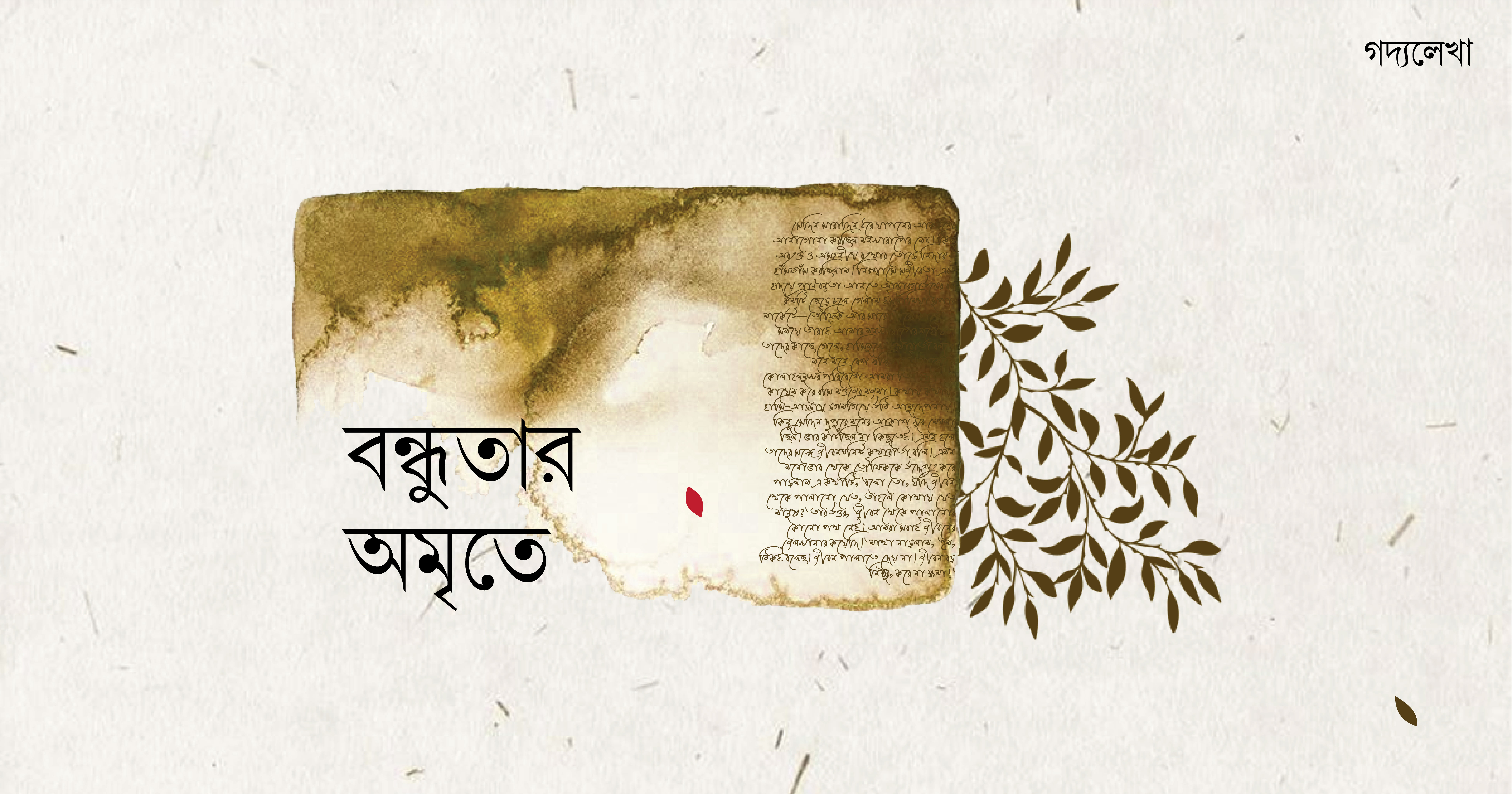রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের নিদাঘ দুপুর। হাওড়ের গেইটওয়ে চামটা বন্দরের ট্রলারঘাটে এসে দাঁড়ালাম। ঘাটলায় দাঁড়াতেই চোখে পড়ল দিগন্ত বিসারিত ঢেউখেলানো হাওড়। টলটলে জলরাশি উত্তাল বাতাসের আশকারা পেয়ে নিদারুণ উচ্ছলিত হচ্ছে। উন্মীলিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে বিস্মিত ও শঙ্কিত হয়ে পড়লাম।
ঘাটলার প্রায় পুরোটা হাওড়ের পানিতে নিমজ্জিত। উপরিভাগের কয়েকটা সিঁড়ি আর খানিকটা পিচ রাস্তা ভাসমান। চামটাঘাটের এমন জলমগ্ন রূপ আরও আগে দেখেছি কি না, মনে পড়ল না। মনে মনে ভাবতে লাগলাম—এখানে যদি এরকম হয়, তাহলে আমাদের বাড়ির দিকে কী অবস্থা হয়েছে জানি! আপাতত ভাবনার বাক্যে পূর্ণচ্ছেদ টানলাম। বাড়ি যাওয়ার তাড়না নিয়ে উঠে বসলাম নৌকায়।
ঢেউখেলানো হাওড়ের বুকে তাগা লাগানো সুঁইয়ের মতো জলসেলাই করতে করতে এগিয়ে চলছে নৌকা। আমি বসেছি গলুইয়ে। নৌকায় উঠলে সবসময় নিজের অধিকার মনে করে এই জায়গাটিতে বসি। এখানে বসে জলজীবনের মোহন দেখতে দেখতে বাড়ি ফিরি। তবে এবার মোহনের সঙ্গে যোগ দিয়েছে অজানা আশঙ্কা। সিলেটের ভয়াবহ বন্যা হৃদয়জুড়ে আতঙ্কের হুল ফোটাচ্ছে।
ভৌগলিক দিক থেকে আমাদের এলাকা সিলেট বিভাগের কাছাকাছি। কিশোরগঞ্জ আর হবিগঞ্জ পাশাপাশি দুটো জেলা। এদিকে লাগোয়া নেত্রকোনা জেলা। ওদিকে এই দুটো আবার সুনামগঞ্জ জেলা লাগোয়া। সিলেটে যে ভয়াবহ বন্যা আঘাত হেনেছে, সর্বভুক্ষু হয়ে খেয়ে নিয়েছে সুনামগঞ্জের আশি ভাগ এলাকা—তা এখন নেত্রকোনা ও হবিগঞ্জ প্লাবিত করে ধেয়ে আসছে কিশোরগঞ্জ হাওড় এলাকার দিকে। আমাদের ধনু নদী—সুনামগঞ্জের বাউলাই নদী থেকে যার উৎপত্তি—এর নাব্যধারা দিয়ে এগিয়ে আসছে সিলেটি বন্যার তোড়, সুনামগঞ্জের সর্বপ্লাবিত বানের জল। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে, এখন মানুষের পক্ষে কোনো প্রতিরোধ সম্ভব নয়।
নৌকার গলুইয়ে বসে বুকভরা শঙ্কা নিয়ে ঢেউয়ের তালে তালে দুলছি। হঠাৎ চোখে পড়ল স্রোতের টানে ভেসে চলা একটি ঢোলকলমির ডাল, তাতে দারুণ আয়েশে বসে আছে একটি জলফড়িং। ঢেউয়ের তোড়ে দুলে উঠছে তার লিকলিকে দেহটি, হাওড় হাওয়ায় ফরফর করে উড়ছে পলকা ডানাদুটো। এই জলজীবনের মোহন দেখে মনের আকাশে ঝলমলিয়ে উঠল ভাবনার তারকারা।
জলফড়িংয়ের বানভাসি-জীবন যেন আমাদের জলমহালের জীবনের প্রতিবিম্ব। হাওয়ার ঝাপটা, ঢেউয়ের তোড় আর স্রোতের ধাক্কার প্রতিকূলতায় একটি ঢোলকলমির ডালকে ধরে যেভাবে অজানা গন্তব্যে ভেসে যাচ্ছে ফড়িংটি—আমরা যারা হাওড়ের বাসিন্দা, জলমহালের জীবনে পড়ে প্রতিনিয়ত এভাবেই ভেসে যাচ্ছি কোথাও না কোথাও। এই বিপন্নতার শেষে কেউ হয়তো খুঁজে পায় আশার কূল আর কেউ বানভাসি-জীবনের কাতরতায় গ্রহণ করে নেয় ভেলার জীবন।
উচ্ছলিত জলরাশির দিকে তাকিয়ে আছি। হাওড় হাওয়ার ঝাপটায় উড়ে যাচ্ছে রোদের দহন। বেশ ফুরফুরে লাগছে। তখনই জেগে উঠল জলশৈশব থেকে মনের মধ্যে পিন হয়ে গেঁথে থাকা সেই প্রশ্নটি— প্রতি বর্ষায় এত বিপুল পানি কোত্থেকে আসে, কোথায় যায়?
ছোটবেলায় যখন বৃষ্টিধোয়া দিনে আকাশের গায়ে রংধনু দেখতাম, তখন সঙ্গীসাথিরা বলাবলি করতাম—এই রংধনু হচ্ছে আকাশের পানির পাইপ। এটা দিয়ে আকাশ-পৃথিবীর পানির লেনাদেনা চলে। বর্ষাকালে এই পাইপ দিয়ে আমাদের হাওড়ে পানি আসে আর শুকনার সময় চলে যায় আকাশে। একটু বড় হয়ে বুঝলাম এই ভাবনা কতটা অলীক। যখন আরেকটু বড় হলাম, পরিণত বয়সের বোধশক্তি অর্জিত হলো, তখনই বুঝতে পারলাম প্রকৃত ব্যাপারটা।
আমাদের এই নদীমাতৃক দেশটি ভাটি অববাহিকায় অবস্থিত। দেশের যত বড় বড় নদী, বেশির ভাগের উৎপত্তি হিমালয় থেকে। নদীগুলো ভারতের বিভিন্ন এলাকা হয়ে আমাদের ভূমি দিয়ে জলের সম্ভার নিয়ে বয়ে যায় বঙ্গোপসাগরে। এজন্য আমাদের দেশ প্রাকৃতিক দিক দিয়ে খুব উর্বর, মনোরম ও ঐশ্বর্যময় এবং ভৌগলিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি। আর এ কারণেই প্রতিবেশী দেশ ভারতের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে নদীগুলোর ওপর—যে কারণে তারা পানির নিয়ন্ত্রণ একতরফা নিজেদের হাতে নিয়ে গেছে। স্পষ্টতই এটা তাদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন।
এমনিতেই আমরা প্রতি বছর নদীর ভাঙনে হেক্টর হেক্টর জমি হারাচ্ছি, ভারত সেগুলো নিজের নামে কাওলা করে নিচ্ছে। আবার এই আগ্রাসনী মনোভাব থেকে বাঁধ বেঁধে রেখেছে নদীগুলোর প্রবেশমুখে। এই ‘হাতে নয় ভাতে মারা’র নীতি থেকে এভাবে তারা পানি আটকে রেখে শুকনার সময় খরায় আর বর্ষাকালে সব পানি ছেড়ে দিয়ে বন্যায় ডুবিয়ে মারছে আমাদের।
হাওড় ছেড়ে নৌকা এবার নদীর মুখে এসে পড়ল। পানির দিকে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে গেলাম। এতক্ষণ যে পানি দেখেছি, তা ছিল কাঁচের মতো স্বচ্ছ; আর এবার যে পানি দেখছি, তা এত ঘোলা যে স্রোতও ঠাওর করা যাচ্ছে না। কৌতূহল দমিয়ে রাখতে না পেরে এলাকার একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘গাঙের পানি এত ঘোলা কেরে?’ সেই লোক জানালেন, ‘সিলেটের বন্যার সব গড়ান গাঙ দিয়া আইতাছে আমরার এইদিগে। এর লাইগ্যে সব পানি ঘোলা অয়া গেছে। এইতা সব বন্যার পানি।’
আরেকটু কৌতূহলী হয়ে আমাদের গ্রাম ও এলাকায় বন্যার প্রকোপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। জানালেন, ‘গেরামের বাজারে পানি উইট্টে গেছে। আলগা যে পাড়াগুলা আছিল, হেইগুলাতেও পানি উইট্টে গেছে। ইটনার দিগে ক্ষয়ক্ষতি অইছে বেশি। সেহানের ম্যালা বাড়িঘরে পানি উইট্টে গেছে। সিলেটের বন্যাডা তো এইদিগ দিয়াই আইতাছে।’ জিজ্ঞেস করলাম, ‘ইটনা-মিঠাইমন-অষ্টগ্রামের যে বিশ্বরোডটা, এইটাতেও কি পানি উইট্টে গেছে?’ বললেন, ‘আরে না, এইডে তো বাক্কা উঁচা সড়ক।’ ও আইচ্ছা বলে তার সঙ্গে আলাপে ক্ষান্ত দিলাম।
আজকের আগে বন্যার যত খবরাখবর সব ফেসবুকে জেনেছি। এরমধ্যে একটা বিষয় খুব চোখে পড়েছে। দেখলাম, সিলেটের ভয়াবহ বন্যার প্রকোপের কারণ হিসেবে অনেকেই দায়ী করছেন ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম অল ওয়েদার রোডকে। বলছেন, এটা অপরিকল্পিত নির্মাণ। হাওড়ের মাঝখানে এই রাস্তা একটা বাঁধের মতো, এর কারণে পানি প্রবাহে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। নেটিজনের বিভিন্ন পোস্ট পেলাম এরকম।
তবে একজন আবহাওয়াবিদ ইঞ্জিনিয়ারের একটি রচনা পেলাম এ বিষয়ে। সেখানে তিনি পুরো ব্যাপারটার পরিষ্কার বর্ণনা দিয়েছেন। সেখান থেকে তা বুঝলাম, তা হলো—এই অল ওয়েদার রোড সিলেটের বন্যার প্রকোপের সর্বাংশ কারণ নয়, প্রাকৃতিক দিক দিয়ে আংশিক হতে পারে। তবে এটা সুপরিকল্পিত নির্মাণ। এর কারণে হাওড়ের পানি প্রবাহে কোনো বাধা সৃষ্টি হচ্ছে না। এই রোডের নিচে পানি চলাচলের জন্য অনেক কালভার্ট দেওয়া হয়েছে, সেইসঙ্গে নদীর ওপরে দেওয়া হয়েছে ব্রিজ এবং শুকনার সময় লোকজনের যাতায়াতের জন্য নিচ দিয়ে ফাঁকা রাস্তা রাখা হয়েছে।
গ্রামের কাচারিঘাটে নৌকা ভিড়ার কথা, কিন্তু সেটি চলে এলো আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে। দেখি সিলেটি বন্যার প্রকোপে মোটামুটি আহত হয়েছে গ্রামটি। বাজারের সড়কটি ডুবে গেছে। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অর্ধেক গ্রাম। লোকজন এখন নৌকা দিয়ে পারাপার করছে। বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, বন্যার ঘোলা পানি ছুঁইছুঁই করছে আমাদের ভিটেবাড়ি। তেঁতুলগাছের তল, বাড়ি এলে যেখানে আমার পাঠবিভোর সময় কাটে, সেখানে এখন কোমর সমান ঘোলা পানি। এই ছায়াবীথিতলে একদল পাতিহাঁস জলকেলি করছে, জলমগ্ন হয়ে আছে একপাল মহিষ।
নৌকা বাড়ির ঘাটে ভিড়তে ভিড়তে তাকিয়ে দেখি, খড়ের পালার আড়াল দিয়ে দেখা যাচ্ছে আমাদের দুচালা টিনের ঘরটি। পুবের জানালায় স্টিলের পাত দিয়ে জাফরি কাটা হয়েছে। এখন এই ঘরে, এই জানালার পাশে শুরু হবে আমার জলবন্দি দিনযাপন।