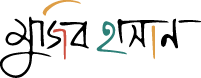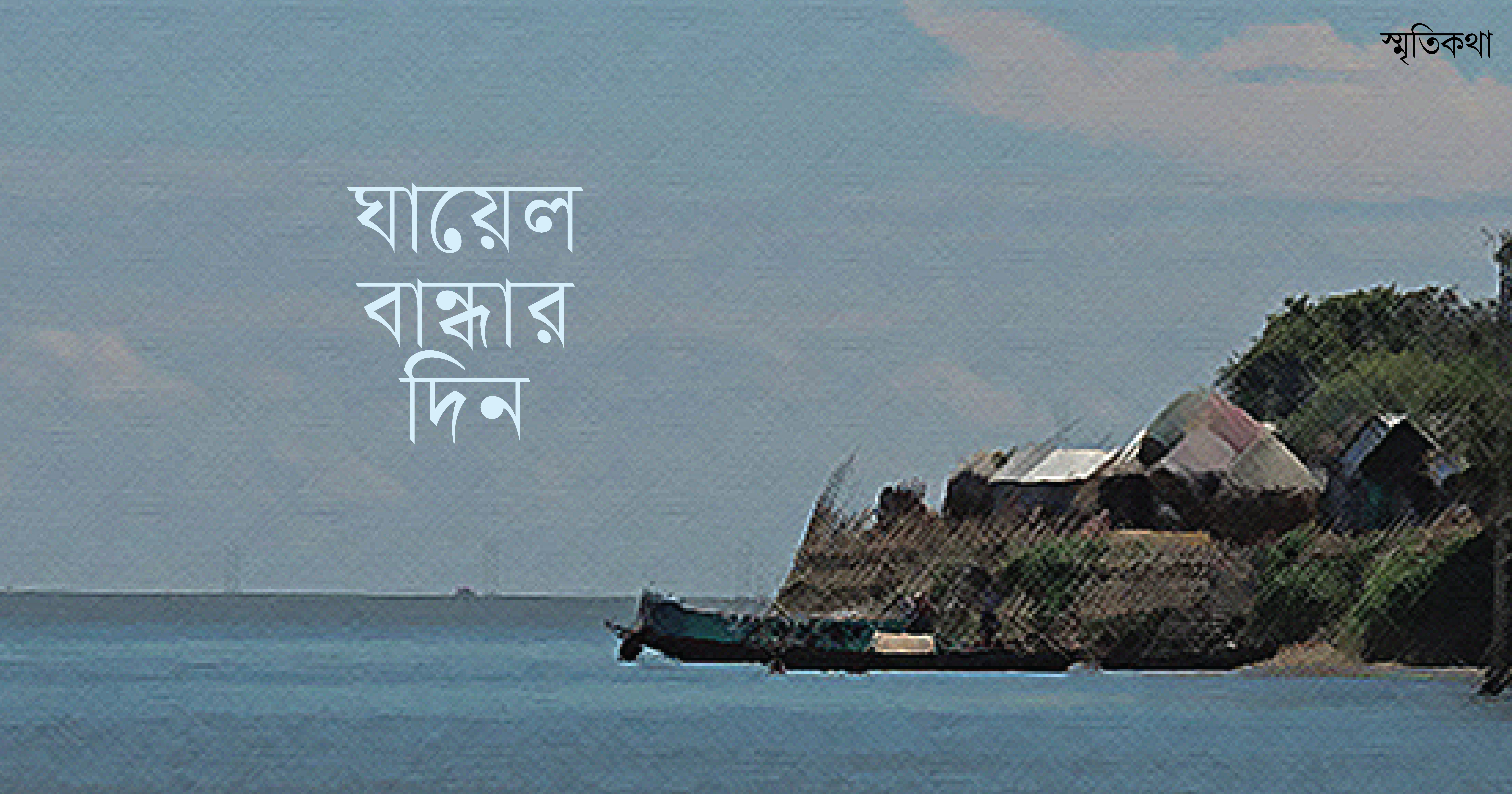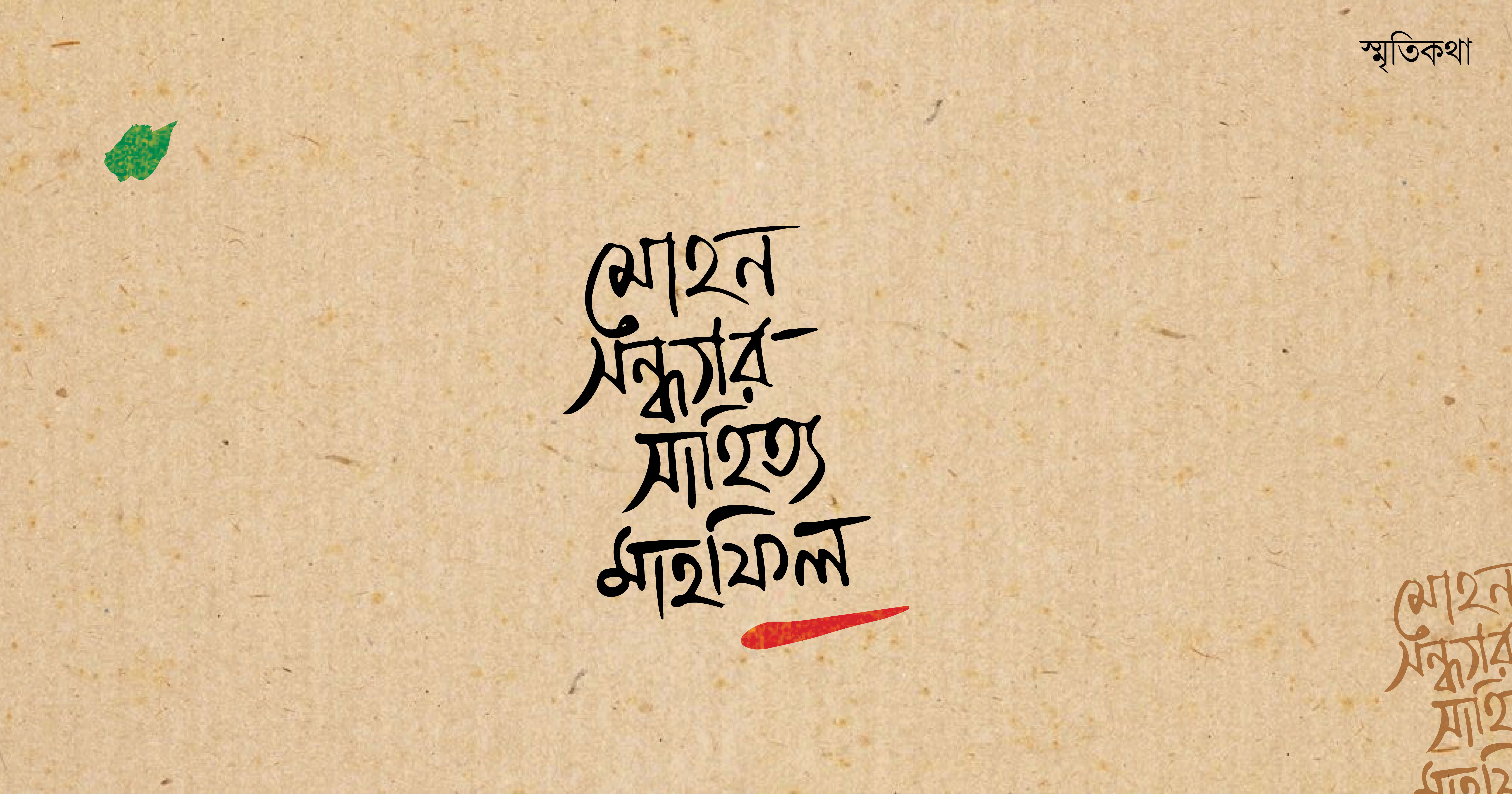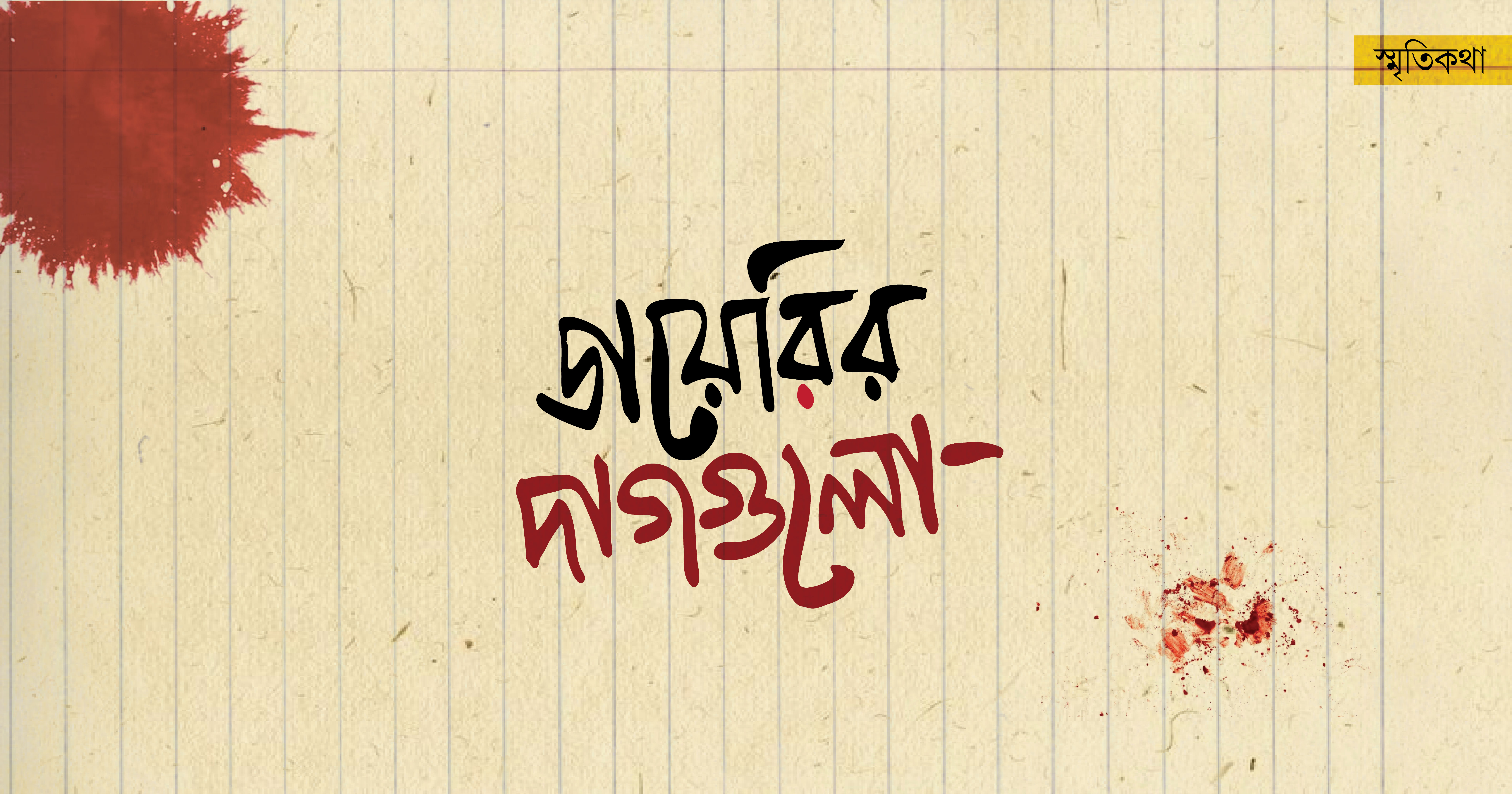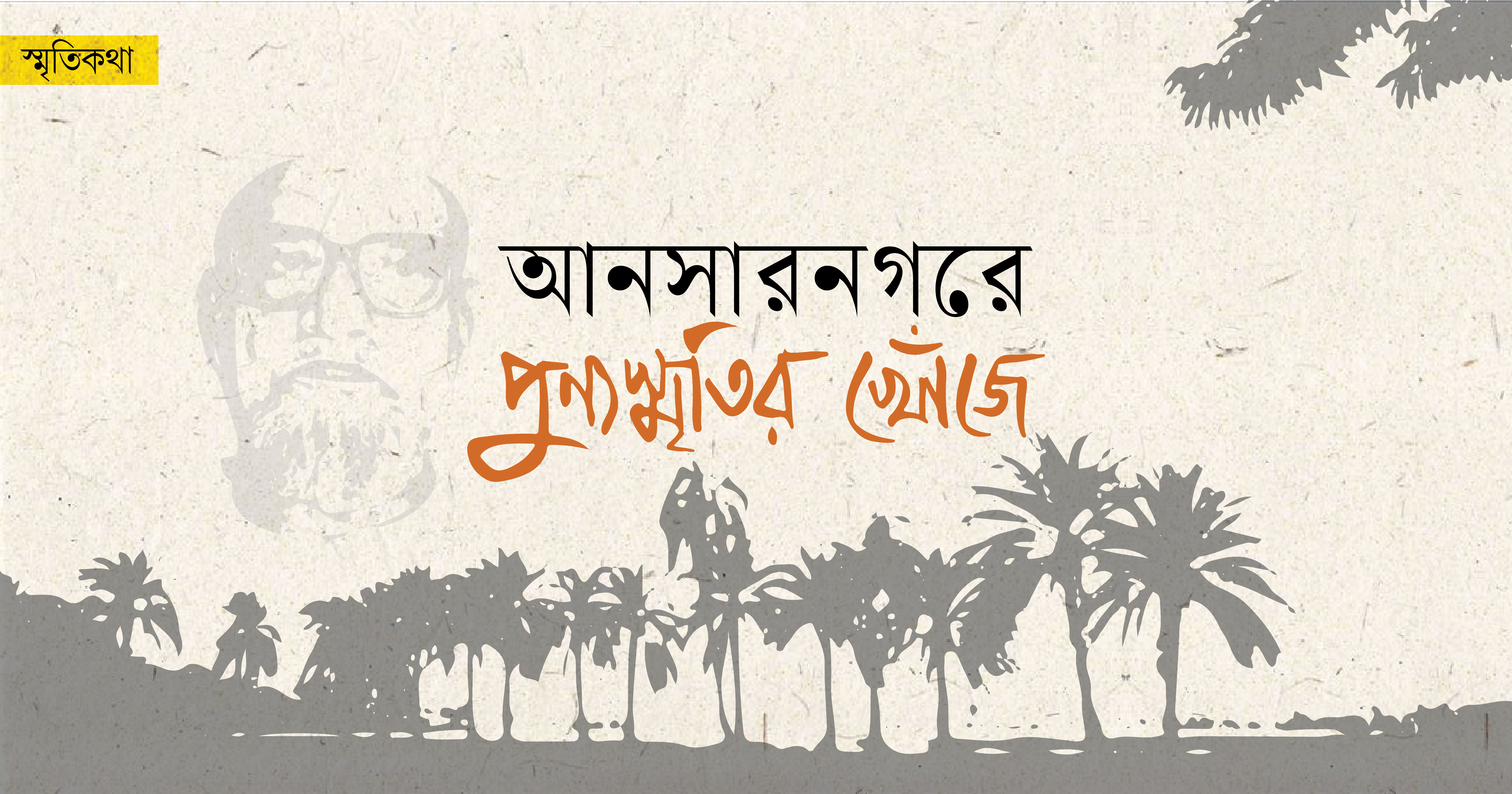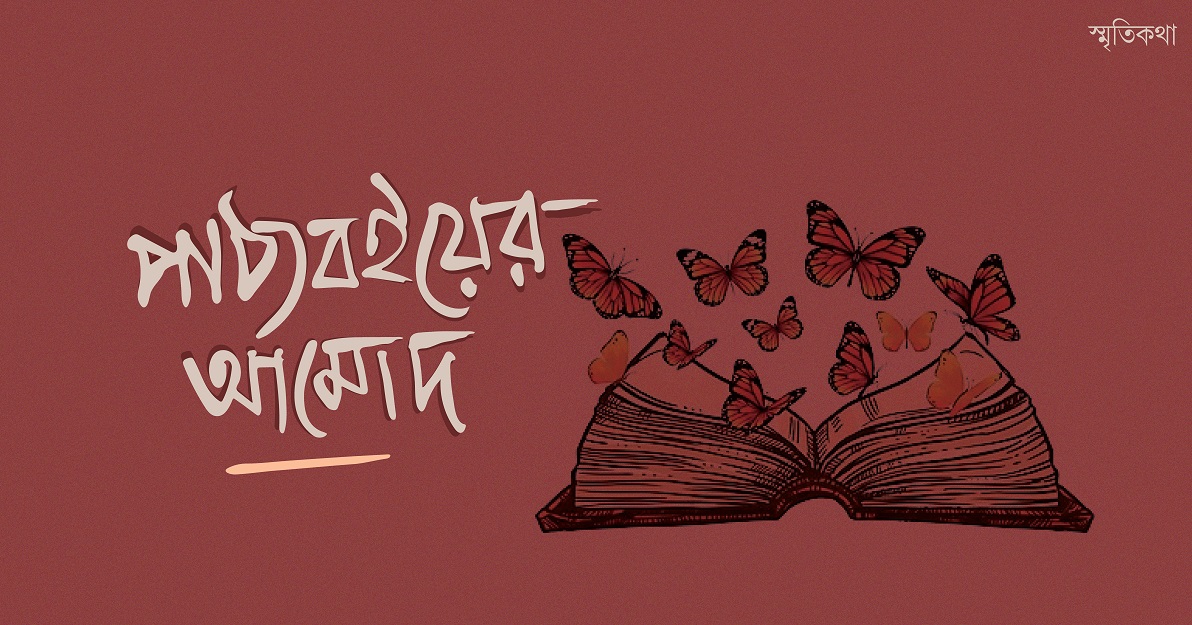আমাদের হাওড় এলাকায় বর্ষাকাল শুরু হয় সময়ের একটু আগে; জষ্টি মাসের মাঝামাঝিতে। কোনো বছর বর্ষা আসে ঠিক সময়ে—আষাঢ় মাসে, আবার কোনো বছর এসে যায় অনেকটা আগেভাগে—বোশেখ মাসের মাঝামাঝি কিংবা শেষের দিকে। তা যেভাবেই আসুক, বর্ষার মরসুমটি কিন্তু হাওড় এলাকার জনজীবনে বিরাট প্রভাব ফেলে।
শুকনা আর বর্ষা—হাওড়ের ঋতু হিসেবে এ দুটোকে ধরা হয়। শুকনা মরসুমে সমস্ত হাওড় হয়ে যায় তেপান্তরের মাঠ। আলপথের বৃত্তে সারি সারি ধানিজমি। এর দোলায়িত সবুজের সঙ্গে হাওড়বাসীর যেন হৃদয়ের সম্পর্ক। অন্যদিকে বর্ষার সময়টায় গোটা হাওড় ধারণ করে বিশাল জলমহালের রূপ। হাওড়বাসীকে তখন যাপন করতে হয় জলের কাছে ইজারা দেওয়া জীবন। সেইসঙ্গে চালিয়ে যেতে হয় ভিটেমাটি আঁকড়ে ধরে টিকে থাকার সংগ্রাম।
বর্ষাকালকে এলাকার ভাষায় আমরা বলি ভাইস্যে মাস। আমার ফেলে আসা জলশৈশবের পুরোটা জুড়ে আছে এই ভাইস্যে মাসের স্মৃতি। হাওড়ের মাঝখানে দ্বীপের মতো ভাসমান যে গ্রামটিতে আমার জন্ম, এ গ্রামের ধরন ছিল লম্বা একটি পাড়ার মতো; এক পাড়ায় এক গ্রাম—যেনবা চিলতে করে কাটা একফালি পাকা পেঁপে, যার পেটের আঁশের সঙ্গে লেগে আছে একরাশ ঘনকালো বিচি।
এরকম পিঠাপিঠি দুচালা টিনের ঘর, হলুদ গম্বুজের মতো খড়ের পালা; বাড়ির সামনে দুয়েকটা আকাশমুখী নারকেল গাছ আর নামায় লাউ, কুমড়া, শিম ও পুঁইয়ের মাচা; বাড়ির পেছনে বিচিকলার ঝোঁপ, ঢোলকলমির ঝাড় আর উঠানের কোণে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বরই প্রভৃতি দেশীয় ফলদ গাছের সমাহার নিয়ে গড়ে ওঠা গ্রাম শিমুলবাঁক। এ গ্রামকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে আমার জলশৈশবের স্মৃতিপুরাণ।
তখন বোশেখের ধানমাড়াই শেষ। খোলায় পড়ে আছে তুষের স্তূপ আর ছোট ছোট খড়ের গাদা। গেরস্তের গোলায় উঠে গেছে সোনার ফসল। সারা বছরের খোরাকি মজুদ। ধানকাম থেকে আজাড় হয়ে কৃষক ও কামলাদের দুয়েক দিনের জিরানো, তারপর বাড়ির সামনে খড়ের পালা—আমরা বলি বনের পুঞ্জি—তোলা নিয়ে শুরু হতো উৎসবের আমেজ।
এ উপলক্ষ্যে বিশাল আয়োজনে মেহমানদারি হতো। গোল আলুর ভাজি, মিষ্টি কুমড়ার সবজি, ডায়মন্ড আলু বা কাঁঠাল বিচি সহযোগে রাজহাঁসের মাংস, শোল বা টাকি মাছ দিয়ে মাষকলাইয়ের ডাল, গরু বা মহিষের দুধ আর সাগুদানা দিয়ে তৈরি পায়েস—আমরা বলি শাশ্নি—গেরস্তের পুঞ্জি তোলার এ জেয়াফত নিমন্ত্রিত-রবাহূত সবাই খেতে পারত।
এরপর দিন পাঁচেকের জিরানো। ততদিনে ফসলহীন ন্যাড়া মাঠের দিগন্তরেখায় দেখা যেত বর্ষার আবাহনী ঝলক। ভাসান পানির জোয়ারে ধনু গাং ফুলেফেঁপে উঠত। সেই পানি আগলপা বিল ছাপিয়ে ন্যাড়াবনে আচ্ছন্ন ধানখেত ডুবিয়ে ভিটেমাটি গ্রাস করার বুভুক্ষা নিয়ে এগিয়ে আসত গ্রামের দিকে। তখনই শুরু হতো ঘায়েল বান্ধার তোড়জোড়। আসন্ন বর্ষার মোকাবেলা প্রস্তুতি আর ষাণ্মাসিক সংগ্রামের বূহ্য রচনা করে দাঁড়িয়ে যেত সবাই।
উত্তাল হাওড়ের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের থাবা আর ভাসান পানির স্রোতের ধাক্কা থেকে ভিটেমাটি আগলে রাখার যে বন্দোবস্ত—হাওড়ের ভাষায় একে বলে ঘায়েল। সাধারণত জষ্টি মাসের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হতো ঘায়েল বান্ধার কাজ। ভাসান পানির স্রোত প্রচণ্ড বুভুক্ষা নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ত খোলায়। তা দেখে নড়ে উঠত গেরস্তের টনক। জায়জিরান ঝেড়ে ফেলে সবাই কর্মোদ্যমী হয়ে উঠত। রসদ সংগ্রহে দলে দলে ডিঙিনাওয়ের বহর নিয়ে যাত্রা করত রাংসাবনের দিকে।
গ্রাম থেকে অনেকটা দূরে, আগলপা বিল পেরিয়ে হাওড়ের মাঝখানে সারি সারি হিজল, করচ ও বরুন গাছ আর নল, খাগড়া, বিন্নে, ছাইল্যা প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদের ঘন ঝোপঝাড় নিয়ে বিশাল জায়গাজুড়ে ওই বন—গ্রামের দিকে সম্পৃক্ত করে আমরা ডাকি শিমুলবাঁকের জংলা। সেখান থেকে সংগ্রহ করা হতো ঘায়েল বান্ধার জলজ উপাদান ছাইল্যা আর বাঁশ কেনার জন্য যেতে হতো চৌগাংগার বাজারে।
জলশৈশবের এক উচ্ছলিত সকালে—আমরা তখন নয়াপানিতে দাপাদাপি করে গোসল করায় মত্ত—দেখতে পেতাম পালতোলা ডিঙিনাওয়ের বহর রাংসাবনের দিকে হাল ধরেছে। নিজেদের বাপদাদা, কাকা-ভাইদের দেখতে পেতাম ওই নৌকাগুলোতে—রাংসাবনে যাবে তারা। দেখে আবদেরে মন নিয়ে এগিয়ে যেতাম। নৌকায় ওঠে গোঁ ধরে বসতাম—আমরাও সাথে যাব। বড়রা মানা করতেন, লোভ দেখাতেন : বকের ছানা, শালিকের ছানা, পানকৌড়ি ও বালিহাঁসের ডিম এনে দেবেন। এ লোভে কেউ নিবৃত্ত হতো, ফিরে যেত গোসলে; কেউ জিদ জিইয়ে বসে থাকত—আমি যাবই।
বড়রা তখন ধাতানি দিতেন, ডরভয় দেখাতেন। এত কিছুর পরও যে বড়দের সাথে যেতে পারত, ও হতো সবচেয়ে ভাগ্যবান। নৌকার গলুইয়ে বসে আমাদের দিকে মুখ করে বিজয়ের হাসি হাসত। আমরা বোকার মতো ফ্যালফেলে চোখে তাকিয়ে থাকতাম আর ঈর্ষায় জ্বলতাম।
মনে মনে ভাবতাম—ইশরে, ও জংলায় গিয়ে কত মজাই না করবে! কত কত বক আর শালিকের ছানার পেছনে ছুট দেবে, বালিহাঁসের বাসা থেকে ডিম হাতড়াবে, তাজা তাজা খাগড়া চিবিয়ে রস খাবে—আমরা সেসবের কিচ্ছুটি করতে পারব না! এসব ভেবে একটু মনখারাপের মতো করে ফিরে যেতাম দাপাদাপির গোসলে। ডুবসাঁতার দিয়ে জলসেলাই খেলতে খেলতে মুহূর্তেই ভুলে যেতাম ওই মনোবেদনা।
পড়ন্ত বিকেলে নৌকাবোঝাই ছাইল্যা আর নলখাগড়ার আঁটি নিয়ে ফিরে আসতেন তারা। আমরা খুশিতে ডগোমগো হয়ে নৌকাগুলোকে বেড় দিয়ে দাঁড়াতাম। নৌকায় উঠে সবার আগে খোঁজ নিতাম—বক বা শালিকের ছানা এনেছে কি না, বালিহাঁসের ডিম কয়টা পাওয়া গেছে? ছোট কাকাকে এ জিজ্ঞাসাটা বেশি করতাম। ছোট কাকা ভাতের বাসনের ভেতর থেকে দুটো ডিম বের করে আমার হাতে দিতেন।
তখন হয়তো পাশের নৌকার কেউ বক বা শালিকের ছানা হাতে নিয়ে আনন্দে আটকানা হয়ে বাড়ির দিকে দৌড় দিয়েছে। দেখে আমার একটু মনখারাপ হতো। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ছোট কাকা সান্ত্বনা দিতেন—কয়েকদিন পরে আবারও জংলায় যাবেন, তখন একটি শালিকের ছানা—ছোট কাকার ভাষায় শারোর বাইচ্চে—আমাকে এনে দেবেন। এটুকু সান্ত্বনায় পুলকিত হয়ে উঠত আমার বালকমন।
হাসি হাসি মুখ করে দাদার কাছে যেতাম। দাদা নৌকার গলুইয়ে নলের আঁটি নিয়ে বসে থাকতেন। এগুলো এনেছেন চাটাই বানানোর জন্য। দাদার বেতশিল্পের হাত বেশ ভালো। নলের বেত দিয়ে সুন্দর চাটাই বানান। এ চাটাইয়ে চলে আমাদের গড়াগড়ি, খাওয়াদাওয়া আর দাদা-দাদির নামাজ ও বিশ্রাম। কাছে গেলে দাদা আমার হাতে দুটো খাগড়া ধরিয়ে দিতেন। কাকার দেওয়া ডিম আর দাদার দেওয়া খাগড়া নিয়ে আমিও খুশিমনে দৌড় দিতাম বাড়ির দিকে।
ততদিনে ভাসান পানির স্রোত খোলা ডুবিয়ে বসতবাড়ির নামায় চলে আসত। তখনই জলোহাওয়ায় মাতাল এক সকালে শুরু হতো ঘায়েল বান্ধার কাজ। প্রথমে ভিটেমাটির নিচ থেকে লম্বালম্বিভাবে বাঁশ পুঁতে ওপরে তোলা হতো, তারপর আড়াআড়ি বাঁশ ফেলে এর ফাঁকে ঘন করে ঠেসে দেওয়া হতো ছাইল্যার আঁটি; মোটা তার দিয়ে বাঁধা হতো এগুলোকে।
এভাবে বসতবাড়ির বরাবর করে বাঁশের খুঁটি গেড়ে কাছি দিয়ে টানা দেওয়া হতো। স্রোতে ভাসা কচুরিপানা আর জলজ উদ্ভিদ জোগাড় করে ফেলা হতো এগুলোর ওপরে। এই বন্দোবস্তের নাম ঘায়েল—হাওড়বাসীর বর্ষা মোকাবেলার দুর্ভেদ্য প্রাচীর, আফালের বিরুদ্ধে ষাণ্মাসিক সংগ্রামের মোক্ষম অস্ত্র।
ঘায়েল বান্ধার দিনকে ঘিরে ভাটিয়ালি জনজীবনে শুরু হয় জলমহালের জীবন—যে জীবন পানকৌড়ির মতো ডানা মেলে পারদ গলানো রুপোলি হাওড়ের ঢেউ ছুঁয়ে উড়ে যায়, অথইয়ে ডুবসাঁতার দিয়ে জলসেলাই খেলে, শামুক-গুগলির ভেতর থেকে ঠোঁটে করে তুলে আনে চিকরা মাছ, স্রোতের টানে ভেসে চলা পানিকোলার ঝাড়ে বসে খুঁজতে থাকে জলমগ্ন বাঁশের কঞ্চি।